প্রকাশিত: আগস্ট ১৭, ২০২২
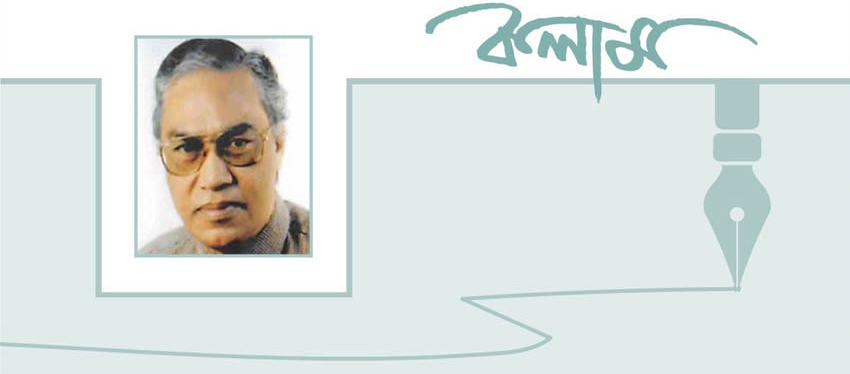
অরূপ তালুকদার
প্রকৃতপক্ষে করোনার পর থেকেই দেশের সাধারণ মানুষকে নানা ধরনের সমস্যা আর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে। বড়-ছোট সবার জন্যই সমস্যাগুলো ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। তবে আমাদের দেশের কিছু অসৎ মুনাফালোভী ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক সুবিধাভোগী নেতা, আমলা এবং ঋণখেলাপি ব্যাংকের অর্থ লুটেরা শ্রেণির মানুষ সাধারণ মানুষদের কষ্ট আর ভোগান্তি অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।
এদের কারণেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে দুর্নীতি। এসব শ্রেণির ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের হাত এখন এতটাই লম্বা যে, অনেক সময় দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও তাদেরকে সহজে ছুঁতে পারে না। তবে এতসবের মধ্যেও একসময় ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা ফিরে আসছিল। সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছিল। যথাসময়ে উদ্বোধন হয়ে গেছে আমাদের স্বপ্নের সেতু, নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু। কিন্তু এর মধ্যেই গত ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গেছে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ। প্রথমদিকে এই যুদ্ধের ভয়াবহতা ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে খুব বেশি উদ্বিগ্ন ছিল না কোনো দেশের মানুষ। কিন্তু ধীরে ধীরে এই যুদ্ধ যতই বিলম্বিত হলো বিশ্বের নানা দেশে তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ভয়াবহ রূপে।
প্রধানত দেখা দিল জ্বালানি সঙ্কট। আর সে কারণেই দিনে দিনে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদির দামও বেড়ে যেতে লাগল অস্বাভাবিকভাবে। মূল্যবৃদ্ধির এই প্রবণতা ঠেকাতে হিমশিম খেয়ে গেল অনেক উন্নত দেশ। ধীরে ধীরে এই ঘটনার শিকার হলো আমাদের দেশও। দেখতে দেখতে বিভিন্ন জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে লাগল দেশেও। তবে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এলো হঠাৎ করে সব ধরনের জ্বালানির ৫০ শতাংশেরও বেশি মূল্যবৃদ্ধির সরকারি ঘোষণার পরপরই।
প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা প্রথমদিকে শুরু হয় ২০২০ সালের করোনাকালে লকডাউন ঘোষণার সময়। হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম বাড়তি চাহিদার কারণে বাড়িয়ে দিতে থাকে।
সেই প্রবণতা তখন থেকে আর কমেনি। বরং দিনে দিনে নানা অজুহাতে বেড়েছে। ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে অর্থাৎ করোনা সংক্রমণের দাপট কমে যাওয়ার পরেও স্বাভাবিকভাবে জিনিসপত্রের দাম কমেনি। এর কারণ ছিল বিশ্ববাজারে প্রায় সব জিনিসের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি। এই মূল্যবৃদ্ধির এক নম্বর ছিল খাদ্যদ্রব্য। এরপর নিত্যদিনের ব্যবহার্য জিনিসপত্র। যেমন- জুতা-মোজা, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাবান, টুথপেস্ট, শ্যাম্পু, কাগজ-কলম ইত্যাদি। তবে দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়েছে এ বছরের শুরুর দিকে।
গত ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মে মাস থেকে ইউএস ডলারের দাম ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়তে থাকে বিভিন্ন পণ্যের দাম। জুন মাসে মূল্যস্ফীতির হার গত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায় চলে যায়। জুলাই মাসে ভোজ্য তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু দ্রব্যের মূল্য কিছুটা কমলেও স্থিতিশীল থাকেনি।
আগস্ট মাসের শুরুতেই এলো বড় ধাক্কাটা। জ্বালানি মন্ত্রণালয় গত ৫ আগস্ট রাতে পেট্রোল ও অকটেনের দাম যথাক্রমে ৮৬ টাকা থেকে ৪৪ টাকা বাড়িয়ে ১৩০ টাকা এবং ৮৯ টাকা থেকে ৪৬ টাকা বাড়িয়ে ১৩৫ টাকা এবং ডিজেল ও কেরোসিন লিটারপ্রতি ৩৪ টাকা বাড়িয়ে ১১৪ টাকা নির্ধারণ করার ঘোষণা দেয়। মূল্যবৃদ্ধি ঘটে ৪২ থেকে ৫১ শতাংশ। এরপরে আবার প্রস্তাব আসছে নতুন করে বিদ্যুৎ ও পানির মূল্যবৃদ্ধির জন্য। অবস্থাটা আসলে তখন কেমন দাঁড়াবে? এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাগলা ঘোড়া এবার কোথায় গিয়ে থামবে। এবারের ধাক্কাটা পৌঁছে গেছে আলু, পটোল, বেগুন থেকে একেবারে লাউ ও পুঁইশাক পর্যন্ত। গত তিন চার দিনে সাধারণ মানুষের খাদ্য এক ডজন ডিমের দাম দিন দিন বেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে ১৬৫ টাকায়। এভাবে প্রায় প্রতিদিনই নানা অজুহাতে বেড়ে চলেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব দ্রব্যের দাম। মানুষ যাবে কোথায়?
জ্বালানি তেলের এবারের এই বড় ধরনের মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা সর্বক্ষেত্রে বলতে গেলে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, এটা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে রাতারাতি বেড়ে গেছে সব জিনিসের দাম। যেন ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’- এর মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং কোটি কোটি খেটে খাওয়া সাধারণ কর্মজীবী ও মজুর শ্রেণির মানুষের ঘাড়ের ওপরে আবার নতুন করে পড়েছে মূল্যবৃদ্ধির খাঁড়া। পাশাপাশি সরকার পড়েছে সমালোচনার মুখে। যদিও সরকার জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণ ও তার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছে। কিন্তু তা মানছে কে? প্রশ্ন যেন একটাই- বিশ্বে জ্বালানির দাম কমছে, আমাদের দেশে কেন বাড়ল? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুব সোজা কি?
জ্বালানি তেলের সঙ্কটের কারণে মূল্যবৃদ্ধির স্বাভাবিকভাবেই বড় ধাক্কা লেগেছে পরিবহন, সেচকাজ এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রে। কারণ এসব খাতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় ডিজেল। পরিবহন ক্ষেত্রে বাস-ট্রাক লঞ্চ ইত্যাদি সবই চলে ডিজেলে। প্রাইভেট কার চলে পেট্রোল বা অকটেন দিয়ে। এখন পর্যন্ত দেশে বছরে যে ৬৫ লাখ টন জ্বালানি তেলের প্রয়োজন হয়, যার মধ্যে আছে প্রায় ৫০ লাখ টন ডিজেল, এর প্রায় পুরোটাই বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এখন যত সমস্যা শুরু হয়েছে এক্ষেত্রেই।
অথচ দেশে প্রতিবছর এই মানুষের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু তাদের চাহিদা অনুসারে উৎপাদন ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে না। যদিও শিল্প-কলকারখানা বাড়ছে তার ফলে বাড়ছে গ্যাসের চাহিদা, কিন্তু এখন সে গ্যাসক্ষেত্রই মহাসঙ্কটে।
ধারণা করা হচ্ছে, নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করা না গেলে আমাদের এখন পর্যন্ত যতটুকু মজুদ আছে তা ২০৩০ সালের মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। তাই আমাদের দেশের বড় বড় শিল্প-কলকারখানা চালু রাখতে হলে ৪০০ কোটি ঘনফুট গ্যাস দরকার হয় এখন বছরে নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।
এদিকে গ্যাসের সঙ্কটও কমছে না। আমদানির পরেও দেশে গ্যাসের বর্তমান বাৎসরিক চাহিদা প্রায় ৪০০ কোটি ঘনফুট সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। সরবরাহ করা যাচ্ছে কমবেশি ৩০০ কোটি ঘনফুট, যার বেশিরভাগই উৎপাদিত হচ্ছে দেশে, যার মূল্য কম করে হলেও ২০ হাজার কোটি টাকা। আমদানি করা হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ ভাগ, কিন্তু তার মূল্য তুলনামূলকভাবে পাঁচগুণ বেশি।
সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধাবস্থার কারণে এর দাম আরও বেড়েছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, বিদেশেও গ্যাস সঙ্কটে পড়েছে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোও। তাই স্বাভাবিকভাবে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর দিকে। আমাদের দেশে কয়েকটি কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে পায়রা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির উৎপাদন ক্ষমতা ১৩২০ মেগাওয়াট। আর এই বছরেই চালু হওয়ার কথা রয়েছে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র। তারপরে আসবে মাতারবাড়ীসহ আরও কয়েকটি কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র।
অবাক হওয়ার কিছু নেই, এখনও আমাদের দেশে ৫০ শতাংশের অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে এই গ্যাস ব্যবহার করে। তবে একটা আশঙ্কার কারণ থেকেই যাচ্ছে যে, এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাবার জন্য বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ কয়লা আমদানির প্রয়োজন পড়বে। সেই বিপুল পরিমাণ কয়লা প্রয়োজনমাফিক আনা-নেওয়া এবং ব্যবহারের জন্য দরকার হবে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ব্যবস্থাপনা। এই বিষয়টা নিশ্চিত করাই হবে সরকারের অন্যতম প্রধান তথা প্রয়োজনীয় কাজ।
দেশে জ্বালানি তেলের সঙ্কট শুরু হওয়ার পর থেকেই বিশেষজ্ঞরা বলছিলেন, এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রে সরকার পূর্ব থেকে সতর্ক এবং সক্রিয় থাকলে এই সময়ে আমাদেরকে এতটা সমস্যার মুখোমুখি হতে হতো না। আমাদের দেশে এলএনজি বা লিকুইড ন্যাচারাল গ্যাস আমদানি শুরু হয় যতদূর মনে পড়ে ২০১৮ সালের আগস্ট থেকে।
সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজে আনা-নেওয়ার সুবিধার জন্য এলএনজি কৃত্রিমভাবে তরল করা হয়ে থাকে। আমাদের আমদানি করা এই এলএনজির জন্য মহেশখালী দ্বীপ সংলগ্ন গভীর সাগরে একটি ভাসমান জাহাজে টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। এলএনজি এখানে আবারও পরিশোধন এবং গ্যাসে রূপান্তরিত করে জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালন করা হয়ে থাকে।
এর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানের ছোট-বড় কলকারখানা, সিএনজি স্টেশনসহ ঘরবাড়িতে নানাভাবে সঞ্চালন করা হয় আমাদের দেশের বিভিন্ন খনি থেকে তোলা গ্যাসও। গ্যাস সঙ্কটের কারণে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই ঘরবাড়ি, বাসস্থানগুলোয় গ্যাস সংযোগ দেওয়া বন্ধ রয়েছে। এখন এই গ্যাস ও জ্বালানি সঙ্কট এবং তার হঠাৎ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশের সাধারণ মানুষের বলতে গেলে নাভিশ্বাস উঠেছে। এই সুযোগ নিয়েছে আমাদের দেশেরই কিছু অসৎ এবং সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ী, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি, ক্ষমতাশালী আমলা এবং ব্যাংক লুটেরা। এদের কাছে বলা যায়, দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ এখন জিম্মি হয়ে আছে। তাদের মুক্তি কবে মিলবে কে জানে! দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এখন কোন পর্যায়ে আছে, তা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং মন্তব্য দেখেই বুঝতে পারি।
অতি সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টে খেলাপি ঋণের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, দেশে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ এবং হার দুটোই বেড়েছে। গত মার্চ মাসের তুলনায় এবারের জুন মাসে এসে খেলাপি ঋণ ১২ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২৫ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা। খেলাপি ঋণের এই পরিমাণ ব্যাংক খাতে মোট ঋণ স্থিতির ৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ। মার্চ মাসে যা ছিল ৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ ও ছয় মাসে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ২২ হাজার কোটি টাকা। এই তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের।
এদিকে ব্যাংকাররা বলেছেন, ঋণ পরিশোধে সক্ষম একটি শ্রেণি আগামীতে আরও ছাড় আসতে পারে এমন প্রত্যাশায় ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধ করছে না। শর্ষের মধ্যের এই ভূত তাড়াবে কে? এই পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নেওয়া যেতে পারে, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সম্ভবত ঠিকই বলেছেন, আর্থিক খাতের দুর্বলতাই আসল খলনায়ক।
লেখক: শব্দসৈনিক, কথাসাহিত্যিক